শুভ চক্রবর্তী
প্রায় কুড়ি বছর আগে এক নির্জন সন্ধায় আমরা জড়ো হয়েছিলাম একটি সিনেমা দেখার জন্য। সিনেমা দেখার সামান্য আয়োজনে ‘দ্য’স্যাক্রিফাইস’ দেখার সুযোগ হয়েছিল। বন্ধুর উৎসাহে, সেদিনটি আজও আমাদের স্মৃতিতে কবিতার মতো দৃশ্য-শব্দে ও শব্দহীনতার একটি প্রতিমায় ধরা আছে,ওই সময়ের আরাধ্য সৌন্দযের আকাশে। আমাদের জীবনে। কিছুটা অগোছালোই ছিল সে মুহূর্ত। মুহূর্তের কবিতা হ’য়ে। এখানে কবিতা কেন বললাম এ প্রশ্ন যে আসবে কারও কারও মনে। আসাটাই স্বাভাবিক। এই যে ক্ষীণ একটা যাপনের টুকরো, সে-ও ওই ছবিটির সঙ্গে একটি অংশরূপে আমাদের কারও কারও মনে আরও একটি অন্তহীনতার জন্ম দিয়েছিল, তা-ও যেন কবিতাই। মনে হতে পারে তাহলে কবিতা কি শুধু লেখাই হয় ? নাকি চোখে দেখা অক্ষর ছাড়াও তার উপস্থিতি আমরা টের পাই কোথাও? লেখার বাইরে গিয়ে কি তার আভা আমরা পাই? যদি এভাবেও হয় তবে কীভাবেই বা সে-কবিতা হয়ে ওঠে মানুষের উত্তরণ। কীভাবে তা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়? এরকম করে কি কখনও ভাবি আমরা? হয়ত ভাবি কিন্ত তাকে বোঝাতে পারি না। এই না-বোঝাটাই তখন সমগ্র জীবনের উৎসাহ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাকে বুঝতে গেলেই হারিয়ে ফেলি প্রাত্যহিক সামঞ্জস্য। তাকে জানতে গেলেই জানার থেকে অজানাকেই জানি বেশি । ঠিক যেমন স্বপ্নকে সে ভাবে বোঝাতে পারি না। পারি কি? হয়ত তার একটা ব্যাখ্যা আমরা খাড়া করি নিজের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সঙ্গে সমন্বয় করে। কিন্তু যেমনটি সে নিজে তেমন করে কি পারি? আর পারি না বলেই কবিতা আমাদের তার দিকে নিয়ে যায় আরও বেশি আরো গভীর বেদনা নিয়ে। তখন আরও বেশি রহস্যময় হয়ে ওঠে আমাদের জীবন। আর সেই জীবনের সঙ্গে পা মেলায় কবিতা। এটুকু বলেই যদি নিজেকে জানতে পারতাম ? যদি ওই রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি। পারি না কি? আনন্দ আমরা পাই না কি? যে আনন্দ আমরা পাই সে এক ভিন্ন আনন্দ। তা বেদনার আনন্দ, আর তাই সেই রহস্যময় জগত-জীবন বেঁধে রেখে আমরা তার দিকেই তাকিয়ে থাকি। কখনও কখনও বলি বিস্ময়। এই যে বিস্ময়ের কথা উঠে এল বলার তাগিদে তা কি নিশ্চিতরূপে কবিতার অনুষঙ্গে? নাকি এর কোনও ভিন্ন স্তর আছে সেই না-বলা যেখানে শুরু তার রহস্যের মাঝে? যখন আমরা কোনও কিছু ভাবিই না সেভাবে, হঠাৎই তার উদয় হয় চমক লাগিয়ে সে বলে যায় যেন এই যে আমি। এই-ই আমি এর বাইরে সে আমি আমি নই। এখানে এই ‘আমি’ শব্দটি, ঠিক চালিত অর্থে যাকে আমরা অহরহ গৌরবে আমি বলে জানি ,তা নয় এখানে সে আমি যতটা গৌরবের সে বেদনারও বেশি সে মৃত্যুরও এবং তার আবহ সৌন্দর্যের ।এই আমি তখন নিজের উর্দ্ধে উঠে আসে সকলের মাঝে। প্রানের ধারায়। এই প্রানধারাই আমির বড়ো আমি। সে কেবল শূন্যতা চায় তবুও আমার আমি এই শূন্যতাকেই একান্ত করে দেখতে চাই। বুঝতে চায় নতুন করে । এইরকম একটি কথা আমরা শুনতে পাই তারকভস্কি র কন্ঠে তখন ‘দ্য স্যাক্রিফাইস’এর চিত্রনাট্য সবে শেষ করেছেন, একটা অস্থির মন তাঁকে তারা করে নিয়ে বেড়াচ্ছে । এই সময় আলোকচিত্রী শ্বেন নিকভিস্ট এর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে নিয়ে লোকেশন সন্ধান করেন স্যাক্রিফাইস এর কাজ শুরু করার জন্য। গটল্যান্ডের কাছে এক দ্বীপে তাঁর পছন্দের জায়গা খুঁজে পেয়ে ওখানেই বাড়িটি তৈরি করাতে চাইলেন। পরবর্তীকালে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন ওখানকার নিসর্গ বিরক্তিকরভাবে একঘেয়ে আর শূন্য, কিন্ত এটাই সেই জায়গা যা তিনি চাইছিলেন। এই শূন্যতাই তাকে আকৃষ্ট করেছিল বারবার। জীবনের সুনিশ্চিত উত্তরণ গুলি থেকে প্রত্যেকবারই হারিয়ে ফেলছেন তাঁর সমস্ত বাঁধন। তবুও কোথাও যে তারকভস্কি ভেতর থেকে একটা শক্তি পাচ্ছিলেন আমরণের। এইরকম একটা তীব্র ব্যথা তাঁকে ছিন্ন করছে জীবনের সবচেয়ে একান্ত ভালোবাসার থেকে।
‘ইভানস চাইল্ডহুড’ অথবা ‘স্টকার’ কিংবা ‘মিররে’র তারকভস্কি থেকে যখন ‘স্যাক্রিফাইস’কে বড় করে দেখি আমরা; (দেখি মানে দেখার একটা অভ্যাসে গড়ে ওঠার একটা বৃত্ত হয়ে ওঠার) মনে হয় কিছু ছাপছবির মতো জলের একটা হালকা প্রলেপ, তার আবেদনে আমার ‘আমি’ সাড়া দিয়ে ওঠে, হাত ধরে নিয়ে যায় জীবনের দিকে কুয়াশার আস্তরণ মুছিয়ে একটা ভোরের আকুল, যেখানে আমি নেমে আসে, যেন আলো গায়ে পড়ার শব্দে তার ঘুম ভেঙেছে। তখনই তো ভেঙে যায় সাজানো একটা খেলাঘর, মনে থাকে না তখন ছবির সঙ্গে এর বিরোধটা কোথায়। এই কি তবে যুক্তিপুঁতির বন্ধন? এই কি তবে কবিতাহীন যাপনের আরও একটা প্রত্যক্ষবাদ, আমাদের জীবনে দানবের মতো আগলে থাকে? কিন্ত এই কি সেই দেখার দেখা? এর কি কোনো মানে আছে সেভাবে? তাহলে কীভাবে একটা কবিতার জন্ম হয়? কীভাবে একটা ভালোবাসা জন্ম নেয়, যা স্পর্শ করা যায় না কোনো শব্দ দিয়ে? ‘স্যাক্রিফাইস’ দেখার পর যে কেউ বলতেই পারেন বড়ো আকর্ষণীয় মোহময় যেন। কেউ বলতেই পারেন অনায়াসে এই হোলো দেখার সুখ তবে আমার মনে হয়েছে এ এক ব্যথার সুখ। তবুও যাঁরা ছবিটি দেখছেন তেমন করে তবুও কি তাঁরা বলার ভিতর কোনও অপেক্ষার মাঝে নিজেকে সেই সুখের সংসারে নিয়ে যেতে পেরেছেন? মনে হয় কারন এখানে যে সুখের কথা বললাম তা শুধু আর সুখ নয় আর তখন সে হয়ে উঠছে জীবন আত্মস্থ। এই কি সেই সুখ যা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত? তবুও আমরা প্রার্থনা করি সমগ্র বিশ্বের সেই সুখ যা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আকুল আবেদন নিয়ে একে আমরা পারিনা এড়াতে। ‘দ্য স্যাক্রিফাইস’ ছবিতে আমরা আমাদের এইরকম একটি প্রার্থনা দেখব। তারকভস্কির এই প্রার্থনা শুধু ছবির প্রার্থনা হয়ে থাকে নি তা হয়ে উঠেছে সমগ্রের প্রার্থনা ছবির মূল চরিত্র আলেকজান্ডারর প্রার্থনা শুরু হয় যখন মনে হয় আমরাও ওই প্রার্থনার অংশ হয়ে তাঁরই সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে সত্যের মুখোমুখি হচ্ছি। ‘শিল্প : আদর্শ স্বরূপের সাধনা’ শিরোনামের একটি লেখায় তারকভস্কি লিখেছেন, ‘মানুষের সাহায্য নিয়ে স্রষ্টা নিজেকে জানতে শুরু করল। এই অগ্রগতির নাম দেওয়া হয়েছে বিবর্তন। এবং তা মানবিক আত্মজ্ঞান অর্জনের কষ্টসাধ্য পক্রিয়ার সাথে যুক্ত। বিশেষ বাস্তব অর্থে বলা যায় প্রতিটি ব্যক্তিই জীবনকে এবং নিজেকে জানতে গিয়ে এই পক্রিয়ার অংশীদার হন; অবশ্য প্রত্যেককেই মানবজাতির অর্জিত জ্ঞানভান্ডারকে কাজে লাগান। কিন্ত তা হলেও, নৈতিক ও প্রথাগত আত্মজ্ঞান অর্জনই হল প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।’ কিন্তু দ্য স্যাক্রিফাইস সে অর্থে আত্মঅর্জনের ছবি হয়ে ওঠে যখন, তখন কি একবারও মনে কি হয় না, যেন কবিতা, যেন উত্তরণ? যদি নিঃশব্দের সংগীত বলা হয় এই ছবি তাহলে? তা বললেও এর অর্থ ক্ষুণ্ণ হয় না। জীবনের জন্যই তো এই ছবি! নয় কি? ছবিটির গড়িয়ে যাওয়ার শুরুতেই দৃশ্য চলাচলে আমাদের ভালোবাসার নির্জনতা ছড়িয়ে দেন তারকভস্কি। যেন একটি স্বপ্ন উথলে উঠে গড়িয়ে পড়ছে আমাদের নরম হৃদয়ে। কেন স্বপ্ন বলছি এই ছবিটি দেখতে গিয়ে কখনও কি ভাবি? না ভাবটা অতোটা জোরালো নয় এখানে। একটা মরা গাছের ডাল কীভাবে রূপকের ঘরে ঢুকে পড়ে, আর আলেকজান্ডারকে তখন মনে হয় জীবনবোধের সমগ্রতাকে আমি’র বাইরে গিয়ে ধরবার চেষ্টা তাঁর সমস্ত ছবি জুড়েই। তখন আমাদের অন্তরমহলে কিছু কিছু দৃশ্য তৈরি হয়, আমাদের অবচেতনে কিছু বিশ্বাস জন্ম দেয় ওই চিত্রপট। কোনও যুক্তি ছাড়াই সেই আচ্ছন্নতাকে আমরা কখনও কখনও বলি কবিতা আর তারকভস্কি বলেন একটু ভিন্নভাবে ‘জীবনের সঙ্গে স্বভাবিক সম্পর্কের কাছে ফিরে আসার একমাত্র উপায়ই হল জীবনের পার্থিব বস্তুগুলির বিপরীতে ব্যক্তির বন্ধনহীনতাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা’ তখন তো আমরা যখন বলি আবার ছবি বা ভিন্ন কোনও শিল্প মাধ্যমে প্রবাহিত একটি বোধ তখন কি মনে হয় না সেই বন্ধনের কথাই বলছি আমরা? ‘দ্য স্যাক্রিফাইস’ নিয়ে বলতে গিয়ে তারকভস্কি জানিয়েছিলেন, ছবিটির ইশারা আমাদের ব্যক্তিস্বত্তার সূক্ষ্ম জায়গাটিকে ঘিরে এমনই এক কথার পিঠে কথা জমে উঠেছে, যা বিশুদ্ধ জীবন চেতনা থেকে আমি’কে সবথেকে কাছে থেকে দেখা একটি পট। হয়ত তিনি আরও বেশী কিছু ভেবেছিলেন। আর তাই তিনি জীবনের সঙ্গে লড়াইয়ের সঙ্গে ভাবতে পারছিলেন ছবিটিতে একটি কবিতা রাখতে।
একজন কবির কাছে এটাই তো প্রত্যাশা থাকে তাঁর দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের। তারকোভস্কি ‘দ্য স্যাক্রিফাইস’ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন, ‘আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল ভালোবাসার অসঙ্কোচ নির্ভরশীলতার ভাবনা – যে একাত্মতা জন্ম নেয় কেবলমাত্র আত্মত্যাগেই। এটা ঠিক, ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা নয়।’ আমরা কি এ-ও মনে করতে পারিনা যিনি শুধু সিনেমা করার জন্য সিনেমা করেন না, তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকাটা যে একটা শুধু নির্ভরতাশীলতা হয়ে জীবনকে আঁকড়ে থাকে তা-ই নয়, তাঁর সঙ্গে শিল্পের যে একটা যোগ রয়েছে এবং সমগ্র জীবনপ্রবাহে সেই সংলগ্নতা আরও বেশী আধ্যাত্ম চেতনাকে সংযত করে। এই শিল্প সম্ভবতা কি কোনো আমি’র কাছে নিয়োজিত! তা কি শুধু বেঁচে থাকা, না একটা মুক্তির পথও? সময়ের ভিতর দিয়ে যে আত্মত্যাগ রচিত হয়, তাকে তো আর তিনি কোনো সময়ে বেঁধে রাখতে চান না! তখন তাঁর জীবনই হ’য়ে ওঠে শিল্পের অংশ। তখন কোনো বন্ধনে জীবন-প্রতিমা আটকে থাকে না। শব্দহীন আবেগের মধ্যেও যে শিল্পীর জীবনকে ভালোবাসা যায়, তারই রূপ-অরূপের অনুভব হ’য়ে ওঠে ‘দ্য স্যাক্রিফাইস”। এইখানে শিল্প একা। সম্পূর্ণ একা। এইখানে সে হ’য়ে ওঠে সহজ একটি যাপনচিত্র। এই জীবন প্রতিমা যখন রূপের ভিতর অন্য একটি সত্তার সন্ধান করতে থাকে, তখন আমাদের মনে পড়ে, কিছু কবিতার প্রতিমাও ‘প্রথম দিনের সূর্য, প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে – কে তুমি, মেলেনি উত্তর।’ জীবনব্যাপী সন্ধানই যেন ঘুরেফিরে আসে আমাদের অবচেতনে। যখন জীবন ফিরিয়ে দেয়, কেবল তখনই কোনো কোনো যন্ত্রণাদায়ক জীবনও হ’য়ে ওঠে কবিতা। কিন্তু ‘দ্য স্যাক্রিফাইস’কে সে অর্থে কবিতার মতো কখনও ব’লব না, আর সেইজন্য এই ছবিটি আমাদের কাছে হ’য়ে উঠতে পারে দৃষ্টিপাঠ, যা কবিতাই মূলত। কেন ‘স্যাক্রিফাইস’ একটি ছবির সঙ্গে সঙ্গে একটি কবিতা হ’য়ে উঠল? কেন একটি অমন দৃষ্টিপাঠ আমাদের অভ্যাসের বাইরে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল? জীবন ভাঙা-গড়ার ফাঁকে ফাঁকে যখন আমাদের প্রাত্যহিক আত্মত্যাগ, ছোট ছোট ব্যথা-ছদ্মবেশ উত্তীর্ণ হয়ে ‘পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়, মহা-অজানার’ তখন? সে কি আর আমি’কে ভালোবাসার দায় খোঁজে? নিশ্চয়ই খোঁজে না। আমি’কে দর-দাম করে দেওয়া-নেওয়ার পালা মিটিয়ে দিতে, সে চায় আমি’কে নিশ্চিহ্ন করে দিতে।
কখনও কখনও মনের গভীরে,তল থেকে আমাদের সাড়া পাওয়া যায় না, কোনো মগ্নতা সেই বিহ্বলতা ছুঁয়েও যায় না, তখন অতীতকে নতুনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার একটা প্রবণতা তৈরি হ’তে থাকে।আমাদের মনে এমন এক শূন্যতায় জীবনবোধের প্রতিমা গড়ে ওঠে। তখন তাকে আলাদা শিল্প বলে মনে হয়না, মনে হয় কবিতাই। কখনও কখনও গানও কবিতার হাত ধরে সৃষ্টির এমন এক খেলায় নিজেকে জড়িয়ে নেয় যে তখন মনে হয় এই সৃষ্টিই তো মানুষ চেয়েছে সবসময়। চলতে থাকে তাঁর এই নিজেকে নিয়ে অন্বেষণ তখন তাকে শুধুমাত্র গান বলেও যেন মনে হয় না, মনে হয় এ যেন শ্রুতিপাঠ, মগ্নতাকে যে ভেতর দিক থেকে জাগিয়ে রাখছে। বাইরের কোলাহল তখন ঢাকা পড়ে যায়। কোনও কোনও গানের শেষে, শেষ নীরবতাটুকুও যেন মনে হয় শেষ না হওয়া দৃশ্যের মতো। কী এক সমন্বয় যেন ছড়িয়ে রাখেন তারকভস্কি তাঁর প্রতিটি শিল্পকর্মে। কেন, কেন এরকম একটি ছায়ার-মায়া তৈরি হয় আমাদের মনে? কোনো শিল্পীর যখন তাঁর উদ্ভাসিত পথটুকু সচেতনতার ভিতর দিয়ে আসে না, আমি’র আমি’তে নিজেকে চিনতে পারে না, তাঁর খেয়াল থাকে না সেইসব নিয়ন্ত্রিত রহস্যময় সিঁড়িগুলো। যখন তাঁর সৃষ্টিসুখ কোনো নিয়মের বেড়া মানেনা। যেখানে সংযত নীরবতা সোনার গল্পের মতো অলীক, কিছু ধুলো রয়ে যায় মনে।
দুই
এমন কি মনে হয় কবিতার খুব কাছাকাছি সেই নীরবতাটুকুও যেন সমগ্র জীবনের অনুভব। মনে হয় সাময়িক নিচুতলার আমি, কখনও কখনও বাইরের দিকে বেড়িয়ে আসতে পারে বলে, হয়ত সেই ক্ষীণ আলোর স্পর্শ, জীবনের কাছে মহার্ঘ্য হয়ে ওঠে। ওইটুকু আনন্দই যেন ভারী মনটাকে আলগা করে দেয় তার বাঁধন। সেই আমি’কে যে ধরা দেয়, সেই তো কবিতার কাছে হাঁটু মুড়ে ব’সে বলে : ‘আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই’ হয়ত তাই সে একসময় অনুভব করে মুহূর্তের আমি’কে বলে : ‘জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই। ‘রূপকের মাধ্যমে আমরা দেখি ভিন্ন কোনও সৌন্দর্যের চলাচল তখন হয়ত। যখন আমরা কবিতা নিয়ে কিছু বলছি বা ভাবছি তখনও। ‘কাব্য অথবা বর্ননার মধ্য দিয়ে চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে আমরা আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করি। ‘প্রতীক বনাম রূপক’ প্রবন্ধের শুরুতেই এইরকম একটি লাইনের পর তারকভস্কি লিখলেন ‘রূপকের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করাই আমার পছন্দ। জোর দিয়ে বলি প্রতিকভাবে নয়, রূপকধর্মিতায়। যেখানে আমরা জানি ‘প্রতীকের একটা নির্দিষ্ট মানে, নির্দিষ্ট বৌদ্ধিক সূত্র আছে। যেখানে রূপক একটা ইমেজ।’ ইমেজের তো কোনও আলাদা করে সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই। আর এই সামান্য ধর্মিতায় আমাদের নিয়ে যায় কবিতার ছায়ায়।
যখন আমরা গান শুনতে শুনতে, অথবা কোনো ছবি বা সিনেমা দেখতে দেখতে, শোনা ও দেখার ভেতর থেকে আমার আমি’কে সরিয়ে রাখি, মনে হয় সেই দেখা ও শোনার বাইরে যে দেখা বা শোনা, তা অন্তরমহলের একেবারে নিজস্ব। যেমন আমরা ব্রেস এর ছবি গুলো দেখলে মনে করতে পারি একেকটি শটের বিস্তার কিভাবে আমাদের কবিতার কাছাকাছি নিয়ে যায়। আর তারপরই তাঁকে ভেঙে ফেলছেন ব্রেস। তখন তার দৃষ্টিদানও ওই ইমেজের ভিতর দিয়ে ঘটে। কখনও কখনও এই দৃষ্টিদানকেই স্মৃতিপাঠ মনে করি। মনে হয় কোনও অর্থহীন সময় আমাদের সময়ের উর্ধে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কি সামগ্রিক শিল্পিত ইমেজের অর্থ উদ্ধার করতেই হবে? এই রকম ভাবতেন কোনও কোনও পরিচালক তাঁদের সিনেমা নিয়ে কথা বলার সময়। কেউ কেউ বলেনও সে কথা ভিন্ন প্রসঙ্গেও। ইমেজকেই মনে করি কবিতা বা কবিতার মতো। এইভাবে রুচিবদলের ধরণ আমাদের নিশ্চিত করতে পারে না আসলে কিভাবে আমরা কবিতা হয়ে ওঠার রহস্যময় জগত থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। কখনও কখনও কবিতাও হ’য়ে উঠতে পারে কারও কারও কাছে ক্ষণকালের স্থাপত্যের ছায়ামাখা ছবি। কিন্তু তাই কি? এভাবে কি নিশ্চিতরূপে বলতে পারে কেউ? দক্ষ পরিচালক অন্যদিকে তাঁর জীবনবোধ দিয়ে মূলত একটিই রচনা করেন, দৃশ্য থেকে দৃশ্যের বাইরে যখন আমরা আমার আমি’র ক্ষুদ্র দেওয়া-নেওয়া ভুলে মেনে নিই নবীন কোনো স্রোতের ধারা, যখন অনুভবের আধার হয়ে ওঠে সেই আমি’র আমি, তখনই তাকে বলি এ-যেন কবিতা। হঠাৎ এই আলো এসে আমি’র ঘরটাকে যেন জাগিয়ে রাখে কত যত্ন করে। সে আঁধারে সে নিজেকেই নিজের ভেতরই অনুসন্ধান করে, কী সেই অনুসন্ধান? কেন আমরা এই অনুসন্ধানে জীবনটাকেও জড়িয়ে দিই? এর কোনো মানে আছে যে একমাত্র জীবন দিয়েই একটা সিনেমাকে দেখা যায়? হয়ত এটা ঠিক নয় যে, আমরা কেমন করে ভাবি। আমরা সিনেমার মধ্যে দিয়ে কি গল্প বলার জন্য উৎসাহ বোধ করছি, ঘটনাটা বড় করে দেখছি কিনা? এইরকম কিছু প্রশ্ন আসে আমাদের। কবিতার কাছাকছি পৌঁছাতে। সেখানে তাঁর ভাষাটা আমাদের প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় না অতটা। কারন সে যে কোনো ভাবভাষা হোক না কেন পাঠক বা শ্রোতা তা নিজের মতো ভেঙে নতুন করে গড়ে নিতে পারেন। এইখানে শিল্প হয়ে ওঠে অনন্তের কান্ডারী।
মহৎ শিল্পীর কাজ কোনো ভাষায় সীমাবদ্ধতা নয়, বরং ভাষাকে ছাড়িয়ে সে শিল্প হ’য়ে ওঠে মানবতার জয়গান। যে স্বচ্ছতা আর স্বচ্ছতম ভাষা থাকে না, তখন মনের সবটুকু দিয়ে সেই শিল্পের কাছে গভীর কোনও সন্ধানের যোগ্যতা অর্জন ক’রতে চাই আমরা। হয়ত অনেক সময় নিবিড়তা আমাদের থাকেনা। কবি’র ব্যবহৃত শব্দ বা সিনেমার দৃশ্যের সংঘাত – তাঁর আবরণটি আমরা ভাঙতে পারিনা। আমরা কবিতাটি পড়তে পড়তে বা কোনও ছবি বা সিনেমা দেখতে দেখতে ক্রমশ বদলে যাচ্ছি, আমার আমি’র থেকে প্রতিটি বিন্দুকে আমি অতিক্রম করছি, আমার অভিজ্ঞতা ও অনুভবের মধ্যে দিয়ে এক সম্পূর্ণতার দিকে, জীবনবোধের দিকে। এই জীবনবোধই কবিতা হ’য়ে ফুটে ওঠে দৃশ্য ও শব্দ অর্থাৎ শব্দ অথবা শব্দহীন দৃশ্যের মাধ্যমে। ‘সাইলেন্স’ কিংবা ‘নস্টালজিয়া’র মতো ফিল্মে, কবিতাই ভর করে আত্মঅর্জনের জন্ম দিয়েছে। একদিকে ‘সাইলেন্স’ যেন ভেতরের আমি’র সঙ্গে বাইরের আমি’র দ্বন্দ্বে হয়ে উঠেছে নিঃস্তব্ধতার কবিতা। অন্যদিকে ‘নস্টালজিয়া’র কবিতার ভেতরে এক অন্য আমি’র সন্ধান জাগিয়ে রেখেছে নিভৃতে বিশ্ব’আমির অন্তরাত্মাকে। যেখানে ‘সাইলেন্স’ মৃত্যুর অতীত, ‘আসলে মৃত্যু বলে কিছু নেই। অবশ্যই মৃত্যুর ভয় আছে, সেই ভয়টা বড় জঘন্য, আর এই থেকেই লোকে প্রায়শই এমনসব কান্ড বাঁধিয়ে বসে, যা তাদের করা উচিত নয়’। যেন ‘সিকনেস আনটু ডেথ’, যেখানে শুধুমাত্র আর দর্শনের গভীরতায় আবদ্ধ না থেকে, হয়ে উঠল বার্গম্যানের দুঃসাহসিক তীর্থযাত্রা। এ যেন আধুনিক কবিতার জীবনবোধ। আর এই প্রত্যয় যখন আমদের আমি’কে মাটিতে নামিয়ে রেখে, একটা অপ্রত্যাশিত জীবনের দিকে এগিয়ে গেলো, তখন মনে হয় আসলে আমরা মৃত্যুভয়কেই সামনে এগিয়ে রাখি। কিন্তু ‘স্যাক্রিফাইস’ এর এই যাত্রা দুঃসাহসিক হলেও, মোটেও সহজ ছিল না। ফিল্মকে কবিতার কাছাকাছি আসতে সময় লেগেছে। জন্মলগ্ন থেকে আজকের পৃথিবীতে যখন আমরা উত্তরণের নানা দিক অর্জন করেছি, তখন শুধুমাত্র কবিতা নিয়ে একটা ফিল্ম, এরকম কল্পনা কি আমরা কখনও করি! যখন একটা ফিল্মের কথা ভাবি, বা ফিল্ম দেখার পর আমরা আমাদের আমি’র সন্ধান কখনও করেছি! সেভাবে এই উন্মোচনের স্বাদ কবিতাপাঠের মতোই কি হতে পারে? এই আত্মানুসন্ধানের পথ আরও জোরালো হলো যখন বার্গম্যানের সঙ্গে তারকোভস্কির একটা সূক্ষ্ম সূত্র খোঁজা শুরু হলো,তাঁরা বার্গম্যানের কিছুই বোঝেননি। অস্তিত্ববাদ কী, তা তাঁরা জানেন না। ধর্মীয় সমস্যার চেয়ে বার্গম্যান কি কিয়র্কেগার্ড এর বেশী কাছাকাছি – বলেছিলেন তারকোভস্কি। তারকোভস্কি জানতেন, কবিতা কীভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁর প্রায় প্রতিটি ছবিকে, আর এমনভাবে দৃশ্যের সংঘাত হয়ে উঠত কবিতা, যা দর্শকের কাছে একটা যাদুঘরের মতো। অনন্ত স্বপ্নদৃশ্যই রচিত হয় সহজ লোকজ ধারায়। কবিতা হয়ে ওঠে চলচিত্রের নতুন ভাষা। বার্গম্যান তারকোভস্কি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, সিনেমা যখন তথ্য নয়, সে স্বপ্ন।সত্যি কি আমরা ওইভাবে মনে করি যখন আমরা স্বপ্নদ্রষ্টা হয়ে ছবিটা দেখি? এই কারণেই সবার চাইতে মহান দৃশ্যকল্প? স্বপ্নগৃহের অভ্যন্তরে সে অতি সাবলীলভাবে ভ্রাম্যমাণ? সে বোঝাতে আসেনা। কীই বা সে বোঝাবে? সে একজন দর্শক। তারকোভস্কি যে একজন কবি, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন আমরা তাঁর ছবিগুলি দেখি।’ সারাজীবন যে ঘরের দরজায় আমি কড়া নেড়ে গেছি, তার ভেতরে সে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়’ বলেছিলেন বার্গম্যান। এইভাবে যখন চলচ্চিত্র নিজের ভাষায় উত্তরণ খুঁজে চলেছে, তখন ভাষাকে আরও গভীরে নিয়ে গেলেন জঁ লুক গদার। তাঁর শেষের দিকের ছবি ‘গুডবাই ল্যাংগুয়েজ’। আপাতদৃষ্টিতে প্রবন্ধ মনে হলেও, প্রতিটি দৃশ্যই কবিতা হয়ে ফুটে ওঠে। ভাষা যে কোথায় আমাদের আঘাত করে এবং ভাষাকে কীভাবে আমরা জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি তা এক ভিন্ন মাধ্যমে দেখিয়েছেন গদার। ‘মিরর’ দেখার পর, কারও কারও এমনই মনে হতে পারে। কেউ ভাবতে পারেন এই সারল্য ছবির উপকরণ? কারও কারও মনে হয় যে ঘটনার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য বিকাশ নেই, এ ছবিতে কিন্তু আমাদের স্থিতি ঠিক এইভাবেই ঘুরেফিরে আসে আমাদের মনে। ‘শৈশব স্মৃতির অত্যাশ্চর্য টুকরোটাকরা ইমেজ ভেঙেচুরে, ছিঁড়েছুঁড়ে, আমাদের টেনে নিয়ে যায় শৈশবের কবিতায়। ‘মিরর’ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আকিরা কুরোসাওয়া বলেছিলেন কথাগুলি। এটা সত্যি যে, কোনো পরিচালকের সিনেমা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা কবিতাই। এইভাবে আমরা কখনও ভেবেছি? হয়ত কেউ কেউ ভাবেন সে কথা। আমাদের দেশে সেই কবিতার ইমেজ ছড়িয়ে রয়েছে সত্যজিৎ বা ঋত্বিক ঘটকের ছবিগুলোতেও। কিন্তু তবুও কি ততটা কবিতা হয়ে উঠেছে আমাদের দেশের ছবি! একটি কবিতা?
তিন
ঘটনা ব্যাখ্যা করার প্রবণতা কি একটুও কমে এসেছে আমাদের সেভাবে? দৃশ্যকে তেমনভাবে ব্যবহার হয়েছে কি আজও? যেন গল্পকে আরও বেশি প্রকট করেই দেখানোর প্রবণতাকেই বড়ো করে দেখছি আমরা। মনে কি হয়না কখনও সিনেমাকে গল্প বলার সহজ একটা মাধ্যম হিসেবে দেখছেন কেউ কেউ? আকস্মিকতাকেই আরও একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে কখনও কখনও, ভাবি তো আমরা ভাবি না কি? ভাবি কিন্তু বাইরের চমক লাগানো পথটি ভুলতে পারি না। আর তাই সেই চমকে নিজেকেও জড়িয়ে নিতে চাই মন। কোনো নির্দিষ্টতাকে চিহ্নিত করা যেন অভ্যাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের সিনেমায়। এই প্রবণতা বড় বেশী দৃশ্যের ক্ষতি করে না কি? কবিতার আসা-যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না কি জীবনের প্রান্তিক ধারাটি? হয়ত আমরা স্বপ্ন দেখার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছি বলে ওইরকম একটা অভ্যাস আমাদের জীবনের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। আত্মোপর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের ভানবার ক্ষণস্থায়ী উপকরণগুলি। এইভাবেই দেখি নির্লোভ দৃশ্য-ভাষাকে আড়াল করে সে। তাহলে কি আমরা প্রত্যক্ষকেই আরও গৌরব চোখে সাজিয়ে তুলব, শুধুমাত্র যুক্তিহীনতার জটিল ভাষ্য বলে? কেউ কেউ ভাবতে পারেন সিনেমায় ঘটনার প্রত্যক্ষই কবিতা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে। এমনকি মেধাদীপ্ত পরিচালকও কখনও কখনও ঘটনার ব্যাখ্যাকে সিনেমার একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করতে পারেন। দৃশ্য-শব্দহীন ছবিও কখনও কখনও কবিতা হয়ে ওঠে। ওঠে না কি এমন কোনও একটি আশ্রয়? এমন কোনও মুহূর্ত যাকে আমরা প্রাত্যহিকের বাইরের আবরণ উন্মোচন করি? হয় কি এরকম কোনও সন্ধিক্ষন? তাহলে কিভাবে তা সম্ভব? যখন আমরা দৃশ্যটার মধ্যে কোনো অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু না পেয়ে ঢুকে পড়ি সাজঘরের তেতলায়, সেখানেই হয়ে ওঠে কবিতা! সাজঘরের তেতলায় যে শিল্পী বসে থাকেন, তাঁরই ভালোবাসায় দৃশ্য-সংঘাতে শব্দহীনতার মধ্যেও ফুটে ওঠে ভাষা, যে-ভাষায় কথা বলে সময় ও তার সম্বন্ধ! এই তবে কবিতার ভাষা? ভালবাসার ভাষা? সেই ভাষা ভারতীয় চলচ্চিত্রে তো দুর্লভ নয়; বরং ভারতীয়দের মধ্যে কবিতাই হয়ে উঠেছে জীবনের ভাষা। এই আমাদের সিনেমার ভাষাও। যাপনের ভাষা। যদিও আমাদের এমন মনে না-হওয়া স্বভাবিক নয়; মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক । আর তখনই কবিতার পরম্পরায় নিজেকে ধুয়ে রাখা যায় আসময়ের শীর্ষে । যে কোনো কাব্যিক ইমেজের উপর ভর করে কখনও কখনও বিশুদ্ধতার জন্ম হয় । এই যে বিশুদ্ধতার কথা উঠলো তা আমরা জানব কি ভাবে? সত্যি কি এমন কোনও সিনেমা ভারতীয় ভাষায় রচিত হয়েছে? কিন্ত সত্যি সত্যি এই যাপনের ভাষা যখন আমরা আমাদের দেশের ছবিতে দেখি তখন? মনে কি হয় আর তখন সে ভাষা আমাদের দেশের শিল্পিদের মন উর্তীর্ন করেনি? সেরকম ছবি আগেও হয়েছে, কবিতাকেই আশ্রয় করেই হয়েছে। আমাদের দেখার দৃষ্টিতে সেভাবে হয়ত তেমন করে ধরা দেয়নি। আমরা দেখছি ‘সুবর্ণরেখা’ ছবিতে ফুটে উঠেছে আমাদের যাপিত ভাষা। যখন সেই ভাষাই ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এ বৃষ্টির দৃশ্যের সঙ্গে মিশে যায়?কয়েকজনের হেঁটে যাওয়া দেখি যখন তখনই তো মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সেই আলো, কবিতার আলো। উন্মোচিত হয় বড়ো মনের দরজা। সে কিছুটা অগোছালো হলেও আমাদের দৃষ্টিপাঠ সম্পূর্ণ হয়না তখনও ।কিছুটা অনভ্যাসের আভা লেগে থাকে সেই দেখায়। মনে কি হয় এরকম? মনে হয় বৈকি, শিল্পীর নিজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার একটা উন্মোচন আমাদের সংযত হতে শেখায় তখন। জীবনের এই বোধ যে প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়ে যায়, ক্ষীণ সময়টুকু নিয়ে যখন ছবিতে মেয়েটি গান গাইতে গাইতে পড়ে যায় চৈতন্যের সামনে, বহুরূপীর সামনে, – এই সামান্য আভাটুকু যেন সম্পদ হয়ে রয়ে যায় আমাদের ভেতর ঘরের তেতলায়। সে-ইতো শিল্পী, যে আপন মনে নিজেরই ভিতর মুহূর্তের আভাটুকু ধরে রাখে তার জীবনের ভাষায়। কবিতার আভাটুকু ধুয়ে দিলে প্রাণের ধারা গতি হারিয়ে ফেলে। মুক্তির পথে শিল্পিত যাপনের অভাবটা যখন প্রকট হয়ে আসে তখন যে সিনেমার ভাষা নিয়ে কথা বলা হল এতক্ষন তা অনেক দূরে এসে গেছে তখন। কবিতাকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে প্রাত্যহিকের ‘আমি’ – কেউ কেউ হয়ত এটাই বলবেন, যারা হয়ত তেমনভাবে শব্দহীন দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত।
এটা সত্যি যে তেমন দৃশ্যভাষা অনুসন্ধানও কখনও কখনও ব্যর্থ হয়ে পড়ে। কখনও গল্পের একটা স্রোত এসে ধুয়ে দিয়ে যায় আমাদের কবিতার প্রতিমার চিহ্ন গুলি-কেউ কেউ এই বলে দৃশ্যভাষাকে কবিতার হয়ে ওঠা থেকে গল্পের গড়ে ওঠা ধারাবাহিতাকে প্রকৃত সিনেমার আখ্যা দিয়ে বসেন, আর এরই আভা ছড়িয়ে পড়ে বর্তমান দৃশ্যভাষায় শব্দহীনতার এপারে অদৃশ্য-পাঠে, দর্শকও গল্পের খাঁজেখাঁজে গুঁজে দেন ভয়ানক হাস্য প্রলেপ, যা সিনেমার পিছনে গড়ে ওঠা দীর্ঘ চলচ্চিত্র ইতিহাসকে আড়াল করে। আমাদের মনও গড়িয়ে যায় ডিটেলের গভীরতায়। গল্প বলার একটা অহংবোধ গড়ে ওঠে কারও কারও মনে তখন। আমাদের মেনে নিতে হয় ‘বালা’ কোনো সিনেমা নয়! ঋত্বিক ঘটকের ‘রামকিঙ্কর’ অসমাপ্ত এই ডকুমেন্ট্রি! যাকে আমরা আজও সিনেমা বলে উঠতে পারলাম না, বা রবার্তো রোসেলিনি’র ‘ইন্ডিয়া’৫৭’কে (‘ইন্ডিয়া মাতৃভূমি’) আমরা ছবি বলে এখনও মনে করতে পারিনি! কেন মনে করতে পারছিনা? কবিতা বলে? কবিতা হয়ে উঠছে বলে? এইসব ছবি কি আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি এখনও? কিন্তু গোদার এই ছবিটি নিয়ে যখন বলেন : ‘ইন্ডিয়া’ গোজ এগেইনস্ট অল স্ট্যান্ডার্ড সিনেমা : দ্য ইমেজ ইজ ওনলি দ্য কমপ্লিমেন্ট অফ আইডিয়া, হুউচ প্রোভোক্স ইট।’ তখন মনে হয় গোদারও আমাদের মনকে না জেনেই এই মন্তব্য করেছিলেন, এইসব ভাবি আমরা? সাধারণভাবে এইসব তথ্যচিত্রের মধ্যেও কি আমাদের জীবনের ভাষা, যাপনের ভাষা ফুটে ওঠে না? মনে কি কখনও এমনও হয় আমাদের? অন্যদিকে যাঁরা এই তথ্যচিত্রকে সিনেমা বলে মেনে নিলেন, সেইসব মানুষের কাছে তথ্যচিত্রই সিনেমার ভাষার সন্ধানে এক আদর্শ আঙ্গিক হয়ে ধরা দিল। এইরকম ভাষা সন্ধানে ছোট ছোট ছবি হয়েছে বিদেশে। এখনও হচ্ছে আমাদের দেশে-বিদেশে। আমরা তা দেখেওছি, তাদের মনও যেন তৈরি হয়ে গেছে ততদিনে, যখন আমরা আমাদের দেশীয় ছবিতে সে-সব ভাবনা আমাদের মনকে প্রভাবিত করতে পারেনি সেভাবে এখনও। পেরেছি কি? হয়ত তেমন গরজও ছিল না সেভাবে কোনও কিছু আত্মস্থ করার। আমাদের মনও বড় কোনো কাজের জন্য কবিতার কাছে পৌঁছাতে পারেনি তাই। হয়ত তেমন কোনও আত্মস্থ আমাদের দৃষ্টির বাইরে থাকলেও বড় কোনো জটিলতার সামান্য সরলতাকে গভীর কোনো যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেননি যে কেউ তা নয় আড়ালে কেউ কেউ সে মুক্তির পথ খুঁজেছেন। ‘দ্য স্যাক্রিফাইসে’র’ বহু আগেই আমরা দেখেছিলাম, ‘মেঘে ঢাকা তারা’ – সামান্য হৃদয় আলো, এইভাবে ভেবেওছেন যে কেউ কেউ সে-সময়। তবুও কি ছবিটিকে জীবনের আলো দিয়ে দেখেছি কখনও? আমির বেড়া টপকে ভেবেছি কি কখনও এই ছবির কবিতা ও মুক্তির পথটি কোথায় স্পর্শ করছে আমাদের জীবনে। যে আলোর স্পর্শে আমরা কেউ কেউ তখনই বলেছিলাম ঋত্বিক ঘটকের এই ছবিটি যেন কবিতা হয়ে উঠেছে। বলেছিলাম প্রাত্যহিক জীবনের উর্দ্ধে উঠে এসে। এই দু’ই ছবির মধ্যে কোথাও কি একটা সম্পর্ক আছে – প্রশ্ন করেছিলাম নিজেকেই। এই কল্পনা আসলে আমাদের অন্দরমহলে যিনি বসে আছেন তাঁরই। এই সাদৃশ্য কল্পনা যেন কোথাও মিলে যাচ্ছে কবিতার নিভৃত হৃদয়ে।
দৃশ্যপাঠের সংঘাতে হয়ে ওঠা মৃত্যুকে ছাপিয়ে প্রচ্ছন্ন কবিতার আভাটুকু যেন ছড়িয়ে আছে ওই দুই ছবিতে। এরকম একটা ভাবনা আমরা ছবির মধ্যে, তার ঘটনার ভিতরে যেমন পাই, ঠিক সেই ঘটনার একটা বাইরের দিক আছে, যেখানে আমাদের চোখের দেখার ওপর যেন কেউ কুয়াশাায় একটা হাল্কা পর্দা টেনে দেয়। সেখানে ঢোকার অনুমতি আমি’র নেই। ভেতর ঘরের আমি’ই যে ঢুকতে পারে তার দেখার দৃষ্টি নিয়ে। সেইখানে ভেতর দিকে ছবির যে লিরিক্যাল উন্মাদনা চলে, তারই মধ্যে আমরা কখনও কখনও টান অনুভব করি বাইরে দাঁড়িয়ে। এইখানে আমাদের মনে হয় এ-যেন কবিতা। আর একটা দমবন্ধ করা আনন্দ আমাদের শরীরে হঠাৎ টান দিয়ে ওঠে, সমগ্র আমি’র দিকে এমন মুহূর্ত কি কখনও কখনও কবিতা বলে মনে করি আমরা? “দ্য স্যাক্রিফাইস”-এ আলেকজান্ডার যখন আত্মত্যাগের জন্য ভেতর আমি’র কাছে নিজেকে নিয়ে যেতে চাইছে, অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতাকেই সে আত্মত্যাগের জন্য আদর্শ পথ মনে করে, সে নীরবতাকেই সত্যের ধারক মনে করছে। কিন্তু এই কথাটুকু বাদ দিয়ে যদি দৃশ্যের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই, আমরা কি সামান্য অনুভব করব না ছিটকে পড়া আলোর মতো কোনো কবিতার আভাটুকু? ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় এমনই কত কত কবিতার আভা আমাদের স্তব্ধ করে দিয়েছে, যেন মুহূর্তের দৃষ্টিপাঠ জীবন লিরিকের অনিবার্যতাকে ভেঙে দিচ্ছে, গড়ে দিচ্ছে – ওইটুকুই কবিতার একমাত্র হয়ে ওঠা।
চার
এই হয়ে ওঠার পরও আমাদের যাপন টুকরোর ভিতর অন্য এক স্রোতের ধারা কবিতাকে ধারণ করে। আশাবাদের শিকড়টা ওই দৃশ্য-কারুকলা ও মহত্ত্বের উপরে যে ভাবনাগুলোর অবস্থান চিহ্নিত হয়, তারই কি সফলতা তবে? ‘আমাদের সভ্যতার নাটকটা গড়ে উঠেছে একটা অসঙ্গতি উন্নয়নের ওপর’ কেউ কেউ ভাবেন এইরকম করে। ‘প্রযুক্তিগত চাহিদাগুলি এবং আত্মার প্রয়োজন সমূহের মধ্যে নিখুৃঁত সৌসাম্যই হলো জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।’ যখন অন্য এক রহস্যময়তায় ভিন্ন এক প্রশ্নের মুখোমুখি হই আমরা। যখন শুনি ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় ওই একটু আশা নিয়ে তার বেঁচে থাকা, সে-ও তো একটি কবিতাই, যখন মেয়েটি ওই খাঁখাঁ দুপুরের মতো মুখটি তুলে আমাদের সামনে তুলে ধরে প্রাত্যহিক মুক্তির পথ, যেন মনে কেউ জীবনের দরজাটা হা-করে খুলে দিল। অপ্রত্যাশিতই ছিল যেন সে খুলে দেওয়ার আহ্বান। তখন কি মনে হয়না ওই তো দৃশ্যের স্তব্ধতা? ওই তো দৃষ্টির বাইরে গিয়ে দেখা। শব্দহীন এক পথে জমিয়ে রাখা শব্দ-নুড়ির চিঠি, তখন বুঝতে অসুবিধা হয়না আসলে তাঁর ওই স্মৃতিটুকু সেই চিঠিখানি। শরতের চিঠিখানি ‘কেন যে জমিয়ে রেখেছিল’ এই প্রশ্ন কি আসে তখন! আসে যে না, তা নয়। তবু মেয়েটি কি সেদিন সত্যি বাঁচতে চেয়েছিল? এই প্রশ্নও আমাদের মনে ছড়িয়ে দেয় কিছু কবিতার প্রতিমা, কিন্তু তারপর? কবিতার সদর দরজা কি তবুও খোলে সে যখন আমাদের মনে খোঁচা মারে : ‘দাদা আমি বাঁচতে চাই দাদা’ আর কেবলই সে চিৎকার আমাদের কবিতার কাছাকাছি নিয়ে যায়, আর ছুঁড়ে ফেলে দৃশ্য থেকে, তখনই মনে হয় ওই শব্দ ও শব্দহীন দৃশ্য সংঘাতের আলোমাখা স্পর্শের দলগুলো খুলে যেতে থাকে আমাদের হৃদয়ের গোপনপুরে। মনে হয় আমাদের ওই দৃশ্য যেন এক সবসময়ের প্রশ্নকে জাগিয়ে রাখে। সে প্রশ্ন কেমন? সে কি আত্নঅর্জনের? সেকি কেবলই আত্মত্যাগের? সেকি মুহূর্তের কবিতাকে ছুঁয়ে থাকবার বিহ্বলতা? না কি শুধু বেঁচে থাকার একটা অভ্যাসকে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে দেখা? কখনও কখনও সেই বিহ্বলতা, এই মৃত্যু আমাদের মনকে অধিকার করে! পথ চলতে চলতে বা তেমন কোনো মুহূর্তের কাছে যদি আসে ওই কবিতায় ভরাট একটা মন, তখন সেই অনিশ্চিত মুহূর্তও কবিতা হয়ে ওঠে।
এইভাবে যদি দেখা যায় কবিতার আত্মার স্রোতে কখনও কখনও মুহূর্তের ব্যাপ্তি ঘটে যায়। যখন আকিরা কুরোসাওয়ার ‘ড্রিম’-এর মতো ছবিতে, স্বপ্ন ও চেতনায় প্রচ্ছন্ন অঞ্চলে এক একটি দরজায় প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেন, কোনও অনিশ্চিত গোলোকধাম যেন একই সঙ্গে সে স্বপ্নগুলো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে রাখছে মহাকালের মুহূর্তকে। স্বপ্নের মায়া এখানে কবিতার মতো করে এসেছে, কিন্তু কবিতা হয়ে উঠেছে তার দৃশ্যহীন হয়ে ওঠার মুহূর্তকে সরিয়ে রাখার মধ্যে দিয়ে। বিষয়হীন করে তোলার যে ভাবনা, তারই ভিতর কবিতা যেন ফুটে উঠছে ক্ষণকালের নিবিড়তায়। কুরোসাওয়া দৃশ্যকে এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যেন সে দৃষ্টিপাঠের ভিতরে কোথাও একটা তীব্র টান – দৃশ্য ও শব্দ এক একটি প্রাকৃতিক প্রতিমা বলে মনে হয়। ভাবি এইভাবে যাপনও কবিতাকে স্পর্শ করে। হয়ত সে ভাবে না হলেও ভারতীয় ছবিতেও এমন কবিতার স্বাদ ছড়িয়ে আাছে বিভিন্ন পরিচালকের সিনেমায়, যা আপাতভাবে বড় ‘গল্পকে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া’ বলে মনে করিনা, কেননা, তা আসলে গল্পকে ভাঙার একটি কৌশলও। একটা আঙ্গিক, যে আঙ্গিকই কখনও গল্পকে মুছে দিয়ে মুহূর্তের গাঢ়তাই এনে দেয়। তখন আর গল্পের দিকে মন পড়ে থাকে না। আর এই না-গল্পের গভীরতাই ফিরিয়ে দেয় কবিতার স্বাদ। তখন ফিল্মে ‘ডল ফেস্টিভাল’, বা ‘স্পিরিট অব ট্রি’র গল্পটা শুধুমাত্র গল্প হয়ে থাকেনা আর। হয়ে ওঠে সভ্যতার অন্য একটা দিক, জীবনের ভিন্ন একটা ধর্ম। যাপনের ভিন্ন একটা মানে। ‘দ্য স্যাক্রিফাইস’-এ এইরকমই একটা ছায়ামাখা-জীবন রচনা করা হয়েছে, যা মৃত্যুর চেয়ে বড় একটা হৃদয়। প্রথম ও শেষ দৃশ্যে যেখানে শুকনো গাছে জল দেওয়া হচ্ছে যখন আমরা দেখি, তখনও কি মনে হয়না এই সেই বিশ্বাস, যা আরও ব্যাপ্তি এনে দেয়! কবিতাকে তখন আর ভিন্ন কোনো অর্থ দিয়ে বুঝতে হয়না।



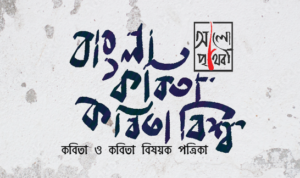
Add comment