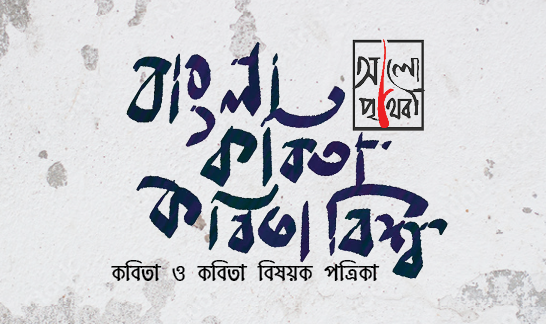
গদ্য : পঙ্কজ চক্রবর্তী
মুখোশের জ্বর অথবা সর্দিকাশি বিষয়ক
তরুণ কবিকে উপদেশ দেওয়ার প্রচলিত মুদ্রাদোষ আজ আমাদের ছাড়তে হবে। এইকথা একজন প্রবীণ কবিকে মনে রাখতে হবে অভিজ্ঞতার মৌখিক উপদেশ চলতে পারে কিন্তু লিখিত সম্পাদনা না করাই ভালো। আপনার পরিমার্জনায় সেটা কবিতা হিসেবে বেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু তা খাতায় বন্দি থাকুক, পত্রিকার পাতায় নয়। অথচ এই পরিমার্জনার আজও বিরাম নেই। তরুণ কবিটি লেখা সম্পাদনার অছিলায় বাড়তি সুবিধা চাইছেন। খ্যাতির একটি শর্টকাট রাস্তায় নেমে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে তার দ্বিধা নেই। পাঠকের ছদ্মবেশে সামান্য দালালি করে সেও প্রবীণ কবিকে দুর্বলতার সুযোগে একটা সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। তাঁকে দিয়ে সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় নন্দনকাননে। জীবনের দুএকটি গোপন মুহুর্তের মালা গেঁথে সেও নেমে পড়ে শিষ্য জোগাড়ের নতুন খেলায়।
নবীন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ \’লেখা\’ আগাগোড়া সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যতীন্দ্রমোহন লিখেছেন \’কাটিয়া- ছাঁটিয়া,মাঝে মাঝে দু চার ছত্র নিজে হইতে যোগ করিয়া\’ কবি তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। আজকে সদ্য লিখতে আসা নবীন কবির এই আমোদ না থাকাই ভালো। বুদ্ধদেব বসু \’কবিতা\’ পত্রিকায় তরুণ কবি শঙ্খ ঘোষের যে কবিতা ছেপেছিলেন তা ছিল আগাগোড়া সম্পাদিত। এতটাই সম্পাদিত যে শঙ্খ ঘোষ নিজের কবিতা চিনতে পারেন নি। কবিতাটি সম্পাদনার ফলে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু সেই কবিতায় তরুণ কবির নিজস্ব আবেগ ও নৈতিক অধিকার ছিল না। অভিমানে শঙ্খ ঘোষ আর কখনও \’কবিতা\’ পত্রিকায় লেখেন নি। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর একটিমাত্র উপন্যাস\’পথের সাথী \’ আগাগোড়া শরৎচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত ও সংশোধিত। দেবেশ রায় অনেক তরুণ লেখকের লেখা সংশোধন করে দিতেন। এলিয়টের কাব্যগ্রন্থ কীভাবে সম্পাদিত হয়েছিল আমি না জানলেও আপনারা হয়তো জানেন ।
আমার পরিচিত মফস্ সলের এক কবি ও সম্পাদকের একটি কবিতায় \’প্রেয়সী\’ শব্দটি বাদ দিতে বলেছিলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। তিনি তা মানেন নি। ফলত \’অলিন্দ\’ পত্রিকায় তাঁর সেই কবিতা ছাপা হয়নি। দুজনেরই আত্মসম্মান আর রুচিবোধকে আমি শ্রদ্ধা করি। এখানে অহেতুক নির্লজ্জ স্নেহ নেই অথবা উল্টোদিকের খ্যাতিলোভী আত্মসমর্পণ নেই। প্রণবেন্দুর একটি কবিতার \’কাম\’ শব্দটি অনিচ্ছাকৃত ভুলে \’কাজ\’ ছাপা হয়েছিল \’শতভিষা\’ পত্রিকায়। সেই বিষাদ থেকেই তিনি হয়তো এই শিক্ষা নিয়েছিলেন। নব্বইয়ের কবিদের একটা বড়ো অংশের কবিতা জয় গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও সংশোধিত। জয়ের কবিতার প্রকট ও প্রচ্ছন্ন ছায়ায় সেইসব কবিতা \’দেশ\’ পত্রিকার রঙিন পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। \’সব এক ধাঁচ,সব এক ছাঁচ কী নিদারুণ দৈন্য।\’ তখন কবিতার যেকোনো পথের শেষ ঠিকানা ছিল গোসাঁইবাগান। জয় গোস্বামীর নিভৃত লালারও অনুবাদ করেছিলেন নব্বইয়ের কবিরা। খুব দ্রুত প্রযুক্তি এসে না পড়লে নব্বইয়ের কবিতা তার স্বতন্ত্র স্বর খুঁজে পেত কিনা সন্দেহ। সদ্য লিখতে আসা তরুণদের \’নিজেরও অগোচরে নিজেরই দিকে টেনে নেবার প্রবণতা\’ প্রায় সব বড়ো কবির মধ্যেই কাজ করে। রবীন্দ্রনাথের ছিল সর্বগ্রাসী প্রভাব। জয়ের ছিল প্রভাব ও প্রতিপত্তি। স্বীকৃতি এবং স্রেফ অস্বীকারের রাজনৈতিক নীরবতা গোপনে অনেকেই টের পেয়েছেন। সেই ইতিহাস কবে আমাদের সামনে আসবে জানি না। আলো ক্রমে আসিবে সে সম্ভাবনা আজও নেই।
সেই কবে পঞ্চাশের শুরুর দিনগুলিতে\’ কৃত্তিবাস\’ দ্বিতীয় সংখ্যার একটি ছোটো গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের কবি ও অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র সরকার। বলেছিলেন \’কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তির বৈঠকখানা\’ থেকে বেরিয়ে আসার কথা। অথচ বাস্তবে হল ঠিক তার উল্টো। পঞ্চাশের অনেক কবির বৈঠকখানা হয়ে উঠল শহর-মফসসলের অনেক তরুণ কবির আশ্রয়। রবিবারের ব্যাগ ভরে উঠতে লাগল নানা কিংবদন্তীতে। অনেকেই পেলেন সৎ পরামর্শ, কবিতা বিষয়ে মূল্যবান পথনির্দেশ। অনেক পেলেন আর্থিক সাহায্য, বিখ্যাত পাক্ষিকে কবিতা প্রকাশের সুযোগ আর পুরস্কারের নমিনেশন। শক্তির সঙ্গে মদ্যপান,সুনীলের অহেতুক স্নেহ আর শঙ্খ ঘোষের সৌজন্যবোধ – স্মৃতির শরীরে নতুন পালকের জন্ম হল। এই আন্তরিকতাকে অনেক তরুণ কবি পরবর্তীতে সার্টিফিকেট হিসেবে কাজে লাগালেন। শঙ্খ ঘোষের নিভৃত ফোনালাপ, দুএকটি ধূসর পোস্টকার্ড সার্টিফিকেটের মহিমায় হাজির হল আমাদের সামনে।
একজন সদ্য লিখতে আসা তরুণ একজন প্রবীণ কবির কাছে আসবে এটাই স্বাভাবিক। শুরুর দিনগুলিতে নানা বিভ্রান্তি,অনিবার্য ডিপ্রেশন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। অনেক ছোটো ছোটো অপমানে লেখা ছেড়ে দেবার কথা ভাবেন অনেকেই। তখন প্রয়োজন শুশ্রূষা, শিষ্য বানানোর ছলনায় অনেক প্রবীণ ভুলে যান সেই কথা। রিলকের মতো তরুণ কবিকে বলতে পারেন না \’আপনাকে উপদেশ দেবার মতো কেউ নেই এবং কেউ আপনাকে সাহায্যও করতে পারবে না।\’ না বললেও মৌখিক সাহায্যটুকু ছাড়া আর কিছু দেওয়ার অধিকার নেই এই বিশ্বাস একজন প্রবীণের থাকা উচিৎ। বড়জোর ছন্দ-মিল বিষয়ে সংশোধন চলতে পারে। কিছু করার বদলে আর একবার তার হাতে তুলে দেওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের \’বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন\’ অথবা শঙ্খ ঘোষের \’তরুণ কবির স্পর্ধা।\’ প্রয়োজনে তার হাতে তুলে দেওয়া যায় রণজিৎ দাশের\’ একটি প্রাচীন ইস্তাহার\’ও। কাজ হয়তো তেমন হবে না। ডেঙ্গু নিবারণের সরকারী নির্দেশ কতটুকুই বা আমরা পালন করি। তবুও যেকোনো উপদেশ দেওয়ার আগে সারিয়ে নেওয়া দরকার একজন তরুণ কবির অসুখ ও ছলনার নানা ছদ্মবেশ। গুরু শিষ্যর সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে অতঃপর আমাদের তেমন কিছু বলার নেই।



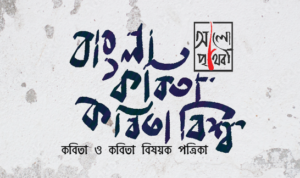
6 comments
অচিন্ত্য রায়
আবার পড়লাম। উপযুক্ত লেখা
সৌরভ সরকার
খুব যুক্তি যুক্ত লেখা । এই ধরনের এডিটিং লেখার ক্ষতি করে যেমন তেমনি প্রকাশের পর কবির মনে অদ্ভুত এক বিষাদ তৈরি করে ।
Mani Biswas
একটা গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট হয়ে থাকল এই লেখাটি।
Unknown
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বপরিচয় একটি অসামান্য কিতাব্।শোনা যায়, কিতাবটির মূল রচয়িতা প্রমথনাথ।গ্রুদেব ভাষা সম্পাদন করিতে করিতে অবশেষে নিজনামেই কিতাবটি প্রকাশ করিয়াছিলেন।কবিতার জগতে এমন উদাহরণ জানিতে পারিলে আনন্দ হইতো।
জা তি স্ম র
পড়লাম। অনবদ্য একটি গদ্য।
Das Ks
আগে পড়িনি। খুব জরুরি লেখা। এবিষয়ে আলোচনা অল্পবিস্তর কোনও কোনও কবির সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে। এই অপকর্মটি এক সময় করতাম খুব কাঁচা বয়সে, লজ্জিত হই এখন। আমার কবিতা 'সংশোধন' করে দিতেন কবি বিশ্বনাথ গরাই। আমি আবার তখন আমার চেয়ে ছোটদের লেখা 'সংশোধন' করতাম। সত্যিই লজ্জিত হই সেই কুড়ি বাইশ বছর বয়সের প্রগলভতায়। সম্পাদনা এক দূরুহ কাজ বিশেষ করে যখন সম্পাদক নিজেও লেখেন। কবিতা পাঠকের কবিতা পড়া, আর সম্পাদকের পড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কবি নিজের মনকে বাঁচাতে চাইলে সম্পাদনা অন্য কারও হাতেই ছাড়া উচিত। কবিতা পাঠকের মন… আমি ভুলও বলতে পারি।